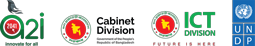রমনা কালীমন্দির
ঢাকার রমনা এলাকায় ছিল হিন্দুদের দশনামী গোত্রের একটি মন্দির। সুউচ্চ চূড়ার এই মন্দিরটি আকারে বেশি বড় ছিল না। ধারণা করা হয়, নেপাল থেকে আগত কালী দেবীর জনৈক ভক্ত মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পরে ভাওয়ালের রানী বিলাসমণি দেবী মন্দিরটি সংস্কার করেন। ১৮৫৯ সালের ঢাকার এক মানচিত্রে মন্দিরটিকে কৃপাসিদ্ধির আখড়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। নাজির হোসেনের বর্ণনায়- “এ মন্দিরের পুরানো নাম কৃপাসিদ্ধি আখড়া, প্রায় সাড়ে চার শত বছর পূর্বে গোপালগিরি নামে ভারতের বদ্রিনারায়ণ থেকে এসেছিলেন এক সাধু পুরুষ। তিনিই এ আখড়ার গোড়া পত্তন করেছিলেন। এখন যে মন্দির আছে সেটি তৈরি করেন হবু চরনগিরি প্রায় আড়াইশ বছর পূর্বে।” ১২টি সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠতে হত। বারান্দার মধ্যখানে কাঠের সিংহাসনে ছিল লাল পাড়ের শাড়ী পরা স্বর্ণ মনি-মুক্তার অলঙ্কারে ভূষিত কষ্ঠি পাথরের কালিক ও ভদ্র কালি মূর্তি। যতীন্দ্রমোহন রায়ের ঢাকার বিবরণ গ্রন্থে লিখেছেন- “এই কালীমূর্তিটি বিক্রমপুরাধিপূত চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি আছে।”
১৮৪০ সালে প্রাচীর ঘেরা রমনা মন্দিরের চূড়ার অলংকার দেখে কর্নেল ডেভিডসন ভেবেছিলেন এটি ক্যাথলিক উপাসনালয়। ভেতর প্রবেশ করে দেখেন কালিমন্দির। তিনি দেখতে পান, দরজার সামনে ছাগল ছানা উৎসর্গ করার গিলটিনের মতো কাঠের একটি যন্ত্র। উৎসর্গ করা ছাগল ছানার মাথাটি মন্দিরের পুরোহিত পায়। শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৫০টির মতো হওয়ায় অন্য রংয়ের ছাগল থেকে কালো রংয়ের ছাগলের চাহিদা ও দাম দু’ই কয়েকগুণ বেশি। ঐতিহাসিক দানীর মতে, “প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে বাদ্রী নারায়ণের যোশী মঠ থেকে জনৈক গোপালগিরি ঢাকা এসে প্রতিষ্ঠা করেন একটি আখড়া। সে সময় এর নাম ছিল কাঠঘর। মূল মন্দিরটি হরিচরণ গিরি নির্মাণ করেন তিনশ বছর আগে। পরে মন্দিরের অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। মূল মন্দিরটি ছিল দর্শনীয়। পুরো মন্দিরটি ছিল পুরানো ইটের দেয়ালে ঘেড়া। দক্ষিণে মন্দিরে প্রবেশের একটিমাত্র দরজা ছিল। ভেতর ঢুকে বাদিকে ছিল একটি চতুষ্কোণ কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ। যার কেন্দ্রে ছিল একটি বেদী। এখানেই ছিল প্রাচীন মন্দিরটি। মন্দিরের ছাদ উঁচু। মন্দিরটি বাংলার চৌচালা ও হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুসারে হলেও এতে মোঘল স্থাপত্য রীতির প্রভাবও লক্ষণীয়। মন্দিরের দরজাটি পাকা। মূল মন্দিরের চূড়া ছিল ১২০ ফুট উঁচু। যা বহু দূর থেকে চোখে পড়ত। মূলত মন্দিরটি কালী মন্দির নামে পরিচিত ছিল।” দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অতীত জীবনের স্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন- “রেসকোর্সের পরিধির মধ্যে যে দুটো মন্দির অবস্থিত, তার মধ্যে পূর্ব দিকের মন্দিরে থাকতেন শিব মন্দিরের পূজারী আনন্দময়ীর স্বামী। পশ্চিম দিকের মন্দিরে থাকতেন আনন্দময়ী।”
রমনা কালী মন্দির লাগোয়া ছিল মা আনন্দময়ীর আশ্রম। রমা পাগলা বা বাবা ভোলানাথ নামে পরিচিত ঢাকার নবাবদের শাহবাগ বাগানের কর্মচারী/তত্ত্বাবদায়ক ‘রমনীমোহন চক্রবর্তী’র স্ত্রী ছিলেন মা আনন্দময়ী। বিয়ের পর আনন্দময়ী ১৩৩১ বঙ্গাব্দে স্বামীর কর্মস্থল শাহবাগে চলে আসেন। আনন্দময়ী কারো কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেননি। ১৩২৯ সালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন আনন্দময়ী নিজেই নিজেকে দীক্ষা দেন বলে জানা যায়। ১৯ বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ/২ মে ১৯২৯ সাল আনন্দময়ী রমনায় প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রম। তার দেশী-বিদেশী ভক্তরা রমনা ও সিদ্ধেশ্বরীর কালীবাড়িতে দুটি আশ্রম নির্মাণ করে দেয়। ১৯৩২ সালে এই দম্পতি উত্তর ভারতের দেরাদুনে চলে যায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন আনন্দময়ী ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেও তার স্বামী এখানেই থেকে যান। তপন কুমার দে গণহত্যা একাত্তর রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম গ্রন্থে লিখেছেন- “...কালী মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে শ্রী মা বলেছেন- ঐ স্থানে যে ভাঙ্গা শিবমন্দিরটি আছে ও একটি ভাঙ্গা শিব আছে, ঠিক সেখানেই কালীর একটি ছোট মন্দির করা হবে এবং যেখানে শিবটি বসানো আছে সেখানেই কালীমূর্তি বসানো হবে। ...রমনা আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী বাংলা ১৩৩৬ সালের ১৯শে বৈশাখ এবং ইংরেজী ১৯২৯ সালের ২রা মে নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে পর্দাপন করেন। ...মন্দিরের ভেতর ছিল শ্রী শ্রী ভদ্রকালীর মূর্তি। সুন্দর কাঠের নির্মিত সিংহাসনে স্থাপিত ছিল ভদ্রাকালী মূর্তি। পরবর্তীতে ভাওয়াল থেকে আনা রাজবাড়ির কালী মূর্তিটি ছিল তার পাশে। মন্দিরের উত্তরপূর্বে ও পশ্চিমে ছিল পূজারী ও অন্যান্য ভক্তদের থাকার ঘর। ভিতরেই ছিল শিব মন্দির। ছিল নাটমন্দির ও সিংহ দরজা। মন্দিরের সামনে ছিল একটি পুকুর। যা আজো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। কালী মন্দিরের সামনের এ পুকুরটা খুবই প্রাচীন।” একাত্তরে পাকবাহিনী রমনা মন্দিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এতে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়।
কালী মন্দিরের উত্তর দিকে ছিল দশনামী সন্ন্যাসীদের মঠ। শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী উদাসীরা মঠটি নির্মাণ করে। এই মঠে ব্যাঘ্রাম্বর পরিধানা চতুভূজা পাষাণময়ী কালীকা দেবী অধিষ্ঠিত ছিল বলে কথিত আছে। মহারাজ রাজবল্লভ মঠটি একবার সংস্কার করেন। পরে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মঠটির শীর্ষভাগ ফেঁটে গেলে সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার করা হয়। এই মঠের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রহ্মানন্দ গিরির নাম। অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধ সাধক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। জানা যায়, অন্তস্বত্ত্ববস্থায় ব্রহ্মানন্দের মাতা দস্যুদের হাতে অপহৃত হন। পথে এক তিলক্ষেতে ব্রহ্মানন্দ জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মানন্দের পিতা এই খবর পেয়ে ছেলেকে তার কাছে নিয়ে যান। দিন দিন ব্রহ্মানন্দের চারিত্রিক দোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে তার মাতা কুলত্যাগী হয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। ঘটনাক্রমে ব্রহ্মানন্দ বেশ্যালয়ে যেয়ে তার মাতার ঘরে প্রবেশ করে। পুত্রের কপালে জড়–লের চিহ্ন দেখে মা তাকে চিনতে পারলে অনুতাপে দ্বগ্ধ হয়ে ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাস নেন। রমনার কালী মন্দিরে এসে দশনামী সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে ব্রহ্মানন্দ গিরি নাম ধারণ করেন। দুষ্কর্মের প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্পে তান্ত্রিক সাধনায় মগ্ন হন। মতান্তরে, সংসার বীরাগি হয়ে ব্রাহ্মণ যুবক ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য রমনায় এসে শ্রীমৎ মাধবানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি মাধবানন্দ গিরি মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে গিরি সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে ব্রহ্মানন্দ গিরি নাম ধারণ করেন। ৫ বছর গুরুর কাছ থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যায়ন ও কঠোর তপস্যার মাধ্যমে সাধন মার্গে যুক্ত থাকেন। এরপর ব্রহ্মানন্দ গুরুর অনুমতি নিয়ে আগম বাগীশ নাগভট্টের কাছে কৌল সাধনার জন্য তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়ে তীর্থ দর্শন শেষে বিক্রমপুরের শ্রীপুরের কাছে কীর্তিনাশা নদী কূলে এক বিরাট পাথর খণ্ডের উপর ধ্যানমগ্ন হন। সে স্থানে তিনি তপসিদ্ধ হয়ে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎ পান। দেবী তুষ্ট হয়ে বর দেয়ার জন্য তাকে বার বার অনুরোধ করলেও তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। শেষে বাধ্য হয়ে তিনি দেবীকে তার ধ্যানে বসার বিরাট পাথরটি মাথায় নিয়ে দেবীকে অনুসরণ করতে বলেন। থামতে বললেই চলে যাবেন এই শর্তে দেবী এতে রাজী হন। ব্রহ্মানন্দ হাঁটতে হাঁটতে মধ্যাহ্নে কয়েকজন ভক্তসহ রমনা কালী মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিছুসময় পর দেবী বলেন ‘ব্রহ্মানন্দ আমি আর অগ্রসর হতে পারছি না। দরজায় পাথর ঠেকে যাচ্ছে।’ ব্রহ্মানন্দ তাকে থামতে বললে শর্তানুসারে পাথর ফেলে দেবী চলে যান। কথিত আছে, এ পাথরটি দীর্ঘদিন রমনা মন্দিরের দরজার পাশে পরে ছিল। ব্রহ্মানন্দ গিরির ‘সিদ্ধিসন’ বলে পাথরটিকে অনেকে পূজা করত। পরে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপুরে ফিরে যান। ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজের পুত্র পরে রমনা মঠের সেবাইত হন এবং এ বংশের শেষ বংশধর মঙ্গল গিরিও এই মঠের সেবাইতের দায়িত্ব পালন করেন। মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হত। কালী মন্দিরের পাশে প্রায় বর্গাকার একটি পুকুর আছে। দানীর বর্ণনায়- “কালীবাড়ীর সামনের পুকুরটা কাটিয়েছিলেন ভাওয়ালের রাণী বিলাসমনি।” ইংরেজ শাসনামলের নথিপত্র সূত্রে জানা যায়, পুকুরটি ম্যাজিস্ট্রেট ডস কাটিয়েছিলেন।
লক্ষ্মীবাজারে রাজাবাবুর ময়দান এলাকায় ছিল রাজাবাবুর বাড়ি ও মন্দির। রাজাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণ প্রসাদ। তিনি ছিলেন ভিখন লাল পাণ্ডে নামের জনৈক ব্রাহ্মণের পৌত্র। আঠার শতকের কোনো এক সময় ভিখন লাল/ভিখন ঠাকুর পাঞ্জাব থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের নানাবিধ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। পরে কোম্পানির দেওয়ান নিযুক্ত হন। ভিখন লাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কাজ পরিচালনা করতেন। এসময় ধনী হয়ে ওঠা ভিখন লাল জমিদারি কিনতে শুরু করেন। তার জমিদারির অন্যতম ছিল নারায়ণগঞ্জের বন্দর। জনশ্রুতি আছে, জনৈক সন্ন্যাসী ভিখনলালকে ৫টি নারায়ণ চক্র দান করেন। এর থেকে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তিটি তিনি তার বসতবাড়ি এলাকা মিয়া সাহেবের ময়দানে স্থাপন করেন। এসময় তার উদ্দ্যেগে ইংরেজদের সহায়তায় ১৮৯০ সালে লক্ষ্মী দেবীর নামে এলাকাটি লক্ষ্মীবাজার নামকরণ করা হয়। লক্ষীবাজারের রাজাবাবুর মন্দিরটি ছিল দোতলা। নিচতলার পুরু দেয়ালে নির্মিত দুটি কক্ষ ও ওপর তলায় নাচঘর ও অন্তরতলা। নাচঘরে কাঠের মেঝে ও দেয়ালগুলো ছিল কারুকাজ মণ্ডিত। পেছনের কক্ষে কাঠ ও রূপার সিংহাসনের ওপর স্থাপিত ছিল লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি। ভিখন লালের সময় এই নাচঘরে নিয়মিত আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করা হত। ভিখন লালের সময় নির্মিত হলেও মন্দিরটি রাজাবাবুর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির নামে পরিচিতি পায়।
ঢাকেশ্বরী মন্দির
সলিমুল্লাহ হল থেকে প্রায় ৬০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে বকশিবাজারে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অবস্থান। ধারণা করা হয়, এটিই ঢাকার আদি ও প্রথম মন্দির। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করে, ঢাকেশ্বরী শব্দ থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি। ঢাকেশ্বরী দেবী ঢাকা অধিষ্ঠাত্রী বা পৃষ্ঠপোষক দেবী। কিংবদন্তি অনুযায়ী, রাজা আদিসুর তার এক রানীকে বুড়িগঙ্গার এক জঙ্গলে নির্বাসন দেয়। জঙ্গলে রানী প্রসব করে পুত্র বল্লাল সেনকে। জঙ্গলেই বেড়ে ওঠে বল্লাল সেন। শৈশবে জঙ্গলের মধ্যে বল্লাল সেন একটি দেবী মূর্তি পান (মতান্তরে, রাজ ক্ষমতায় বসার পর এই জঙ্গলে তিনি মূর্তিটি পান)। বল্লাল সেন বিশ্বাস করতে শুরু করে জঙ্গলে সকল বিপদ-আপদ থেকে এই দেবী দুর্গাই তাকে রক্ষা করছে। পরে বল্লাল সেন রাজ ক্ষমতায় অসিন হলে তার জন্মস্থানে যেখানে দেবীর মূর্তি পেয়েছিলেন সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটি জঙ্গলে ঢাকা অবস্থায় পেয়েছিলেন যায় বলে দেবীর নাম হয় ‘ঢাকা+ঈশ্বরী’ বা ‘ঢাকেশ্বরী’। মন্দিরটিও পরিচিতি পায় ‘ঢাকেশ্বরী মন্দির’ নামে। অপর কিংবদন্তি মতে, লাঙ্গল বন্দের স্নান সেরে ফেরার পথে রাজা বিজয় সেনের রানীর গর্ভে জন্মে বল্লাল সেন। সিংহাসনে বসার পর জন্মস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বল্লাল সেন নির্মাণ করেন এই মন্দির। এই বল্লাল সেন ইতিহাসের সেন বংশের বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। ঢাকার ইতিহাসে পরিচিত বল্লাল সেনকে অনেকে নিহ্নিত করেছেন আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মলহন ওরফে হোসেন শাহ্র পুত্র ও আরাকানরাজ শ্রীসুধর্ম রাজার ভাই মঙ্গল রায় হিসেবে। আরাকান রাজ্য থেকে তাকে বিতাড়িত করা হলে তিনি ঢাকায় আশ্রয়প্রার্থী হন।
মানসিংহ ১৫৯৪-১৬০৬ সাল পর্যন্ত তিন দফায় বাংলার সুবেদার থাকাকালে সংস্কারের অভাবে মন্দিরটির জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে এর সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। এসময় তিনি মন্দির প্রাঙ্গণে ৪টি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পাশাপাশি চারটি শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন। তবে মানসিংহ মন্দিটির সংস্কার করেছিলেন এমন সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। এফ বি ব্রাডলী বার্ট ১৯০৬ সালে রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ণ ক্যাপিটেল নামক গ্রন্থে লিখেছেন- “বর্তমান মন্দিরটি ২০০ বছরের পুরনো ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক হিন্দু এজেন্ট নির্মাণ করেন।” সম্ভবত ভদ্রলোক মন্দিরটি সংস্কার করেছিলেন।
ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রাপ্ত ইতিহাসের প্রায় সবই কিংবদন্তি। এসব কিংবদন্তির সত্যতা নিয়ে মতভেদ আছে। মোগল পূর্ব স্থাপত্যরীতিতে চুন-বালির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। সে থেকে ধারণা করা হয় মন্দিরটি মোগল শাসনামলে নির্মিত। আবার মন্দিরের পুকুর, বাগান, মঠ, মণ্ডপ, সন্ন্যাসীদের আশ্রম, পান্থশালা, অশ্বত্থবৃক্ষ, গর্ভগৃহ সবই আরাকানিয় বৌদ্ধ মন্দিরের সঙ্গে মিলে যায়। মন্দিরের দশভুজা দেবী ও চতুর্ভুজ দেবের যুগল মূর্তিও মগদের তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক। দশভুজা মূর্তিটিকে অনেকে মগদের দেবী বলেও মনে করেন। মগরা সাধারণত নাথদের নামকরণ করে স্থান-জাতি ইত্যাদি নামের শেষে নাথ, ঈশ্বর, ঈশ্বরী ইত্যাদি শব্দ যুক্ত করে। এই সূত্রে ঢাকেশ্বরী নামের উৎপত্তির পেছনেও ঢাকার সঙ্গে ঈশ্বরী শব্দটি যোগ হয়ে এর নাম হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ড. রতনলাল চক্রবর্তীর মতে, “এর নির্মাণ-শিল্প ও গঠন-প্রণালী বৌদ্ধ মঠের মতো। ...সম্ভবত এটি পূর্বে ছিল বৌদ্ধ মন্দির, পরে যা রূপ দেয়া হয় হিন্দু মন্দিরে।” এই তত্ত্বের ওপর তিনি অনুমান করেন এটি নির্মাণকাল দশম শতকে।
ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রাঙ্গণে কয়েকটি মন্দির ও এর সংলগ্ন সৌধ। দু অংশে বিভক্ত মন্দিরের পূর্বদিকে প্রধান মন্দির, নাট মন্দিরসহ কয়েকটি ইমারত। আর পশ্চিম অংশে কয়েকটি মন্দির, পান্থশালা, কয়েকটি কক্ষ ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি একটি প্রাচীন দীঘি (পুকুর)। দীঘিটির চারদিকে ছিল পায়ে চলা সরু পথ। দীঘি ও বিশ্রামাগারের পূর্ব পাশে সাধুদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কয়েকটি অজ্ঞাত সমাধি ও একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশের সিংহদ্বারটি নহবতখানা নামে পরিচিত। পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে পূর্ব-পশ্চিমে একটি উঁচু মঞ্চের ওপর এক সারিতে সম-আয়তন ও একই রকম দেখতে পরপর ৪টি পৃথক মন্দির। প্রতিটি শিব মন্দিরে প্রবেশের জন্য আলাদা সিঁড়ি আর উত্তর দিকে ছাড়া অপর তিনদিকে সরু প্রবেশপথ। এক কক্ষ বিশিষ্ট বর্গাকার মন্দিরগুলোর প্রতিটিতে একটি করে শিবলিঙ্গ। কক্ষগুলোর উপর মঠের মতো চূঁড়াগুলো ঢালু ছয় স্তরে পিরামিডাকারে ওঠে পদ্মপাপড়ির উপর কলসে শেষ হয়েছে।
উত্তরদিকের কেন্দ্রীয় মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। তিনকক্ষের মন্দিরটির মাঝের অংশটি আয়তকার আর পার্শ্ববর্তী দুটি বর্গাকার। মন্দিরের সামনের বারান্দাও অনুরূপ তিন অংশে বিভক্ত। কক্ষ ও বারান্দার প্রতি অংশের সামনের দিকে একটি করে খিলান প্রবেশপথ। কক্ষগুলোর ওপর অনেকটা চৌচালা ঘরের মতো ছাদ ; তার উপর ভারতের উত্তরাঞ্চলের মন্দিরের আচ্ছাদনের মতো তিনটি ধাপ। এই ধাপের উপর মন্দিরের প্রত্যেক কক্ষের উপর একটি করে তিনটি পিরামিড আকারের শিখর চূড়া। মাঝের চূড়টি তুলনামূলক উঁচু ও বড়। হৃদয়নাথ মজুমদারের বর্ণনায়- “মন্দিরটি পঞ্চরতœ, সামনে নাটমন্দির। নাট মন্দিরকে ঘিড়ে আছে এক সারি কক্ষ। আর রয়েছে একটি বড় পুকুর, নহবতঅলা ফটক যার ভেতর দিয়ে হাতি যেত। পূর্ব দিকে রয়েছে কয়েকজন সাধুর সমাধি যারা একসময় মন্দিরে পূজা বা ধ্যান করতেন। মন্দিরের বাইরে আছে ৫টি (৪টি) মঠ, প্রতিটিতে একটি শিবলিঙ্গ। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত প্রতিদিন এর পূজা করেন। জনশ্রুতি রয়েছে, বল্লাল সেন দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই তোরণপথে হাতির পিঠে করে মন্দিরে প্রবেশ করেন।” কেন্দ্রীয় কক্ষের ভেতর উভয় পাশের কক্ষে একটি করে কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ। কেন্দ্রীয় কক্ষে একটি চতুর্ভুজ দেবমূর্তি (বাসুদেব) ও মন্দিরের মূল দেবী দশভুজা (ঢাকেশ্বরী/দুর্গা)। কথিত আছে, দশভুজা মূর্তিটি সোনার তৈরি। অবশ্য অনেকে এটিকে অষ্টধাতুর বলে মনে করেন। জানা যায়, মূর্তিটির একটি প্রতিরূপ বানাতে গিয়ে মানসিংহ বিপত্তিতে পরেন। নির্মিত মূর্তিটি এতোটাই সাদৃশ্য হয়েছিল যে কারিগররাই আলাদা করতে পারেনি প্রকৃত মূর্তি কোন্টি। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় বারভুঁইয়া গ্রন্থে লিখেছেন- “পরে তত্রত্য কর্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্তির অনুরূপ হিরন্ময়মূর্তি নির্মাণের জন্য নিয়োগ করিয়া, তাহারা পাশে কোনোরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্য সর্বদা রক্ষিগণকে তত্ত তালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্য প্রতিমা নির্মাণ করে। যে দিবস কাজ শেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া বলে, মহারাজ আমরা এইবার এই নবনির্মিত দেবীমূর্তি পুকুর থেকে স্নান করে আনতে ইচ্ছা করি। রাজা তাদের কথায় স্বীকৃত হয়, নির্মাতারা অলক্ষিতে তাদের নির্মিত মূর্তিটিকে দেবীর আসোনোপরি রেখে যথার্থ দেবিমূর্তিকে মেজে-ঘেষে স্নান করিয়ে আনে, পরে উভয় মূর্তি একই হলে দুই মূর্তির মধ্যে বিভেদ করা কঠিন হয়ে পরে। নির্মাতারা এই কথা প্রকাশ করলে মানসিংহ তাদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে চাদরায়ের দেবিকে জয়পুরে নিয়ে যান ও অপর মূর্তিটি ঢাকাতে স্থাপন করেন। এটিই ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত।” প্রবন্ধকার যাকারিয়ার মতে, “মন্দিরের মূর্তিটি ১৭ শতকের নির্মিত, তার আগের নয়।” প্রধান মন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নাট মন্দির তারপর যজ্ঞ মন্দির। একসময় পাঠাবলি দেয়ার জন্য মণ্ডপের একটি স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরটিকে ঘিড়ে বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ব্যাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে। একসময় গ্রামাঞ্চলের উৎপাদকরা তাদের পণ্য নিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে উপস্থিত হত ; বিনিময়ের মাধ্যমে একে অন্যের কাছে তা আদান-প্রদান করত। তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এই মন্দিরে আলোচনা করত।
[বল্লাল সেন : বাংলার সেন বংসের দ্বিতীয় রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৬০-৭৮ সাল। অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, রাজত্বের প্রথম সময় বল্লাল সেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থে লিখেছেন, পিতা বিজয়সেনের শাসনামলে বল্লালসেন মিথিলা জয় করেন। তিনি প্রায় ১৮ বছর সাফল্যের সঙ্গে রাজত্ব করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র লক্ষণসেনকে রাজ্যভার অর্পণ করে সস্ত্রীক (তার স্ত্রী চালুক্য রাজকন্যা রামদেবী) ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ লেখক। তার রচিত গ্রন্থ দানসাগর (১১৬৮), উদ্ভুতসাগর (১১৬৯, অসমাপ্ত) গ্রন্থ দুটিতে গৌড় রাজার সঙ্গে বল্লাল সেনের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বর্ণিত আছে। শিবের উপাসক বল্লাল সেন অন্যান্য রাজকীয় উপাধির সঙ্গে অরিরাজ নিঃশঙ্ক শঙ্কর উপাধি নেন। তিনি ১১৭৯ সালে মারা যান।